বাক্য প্রকরণ
ভাষার মূল উপকরণ হলো অর্থবোধক বাক্য এবং বাক্যের মৌলিক উপাদান হলো শব্দ।
বাক্য কাকে বলে?
বাক্য — যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে
প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে।
কতগুলো পদের সমষ্টিতে বাক্য গঠিত হলেও যে কোনো পদসমষ্টিই বাক্য নয়। বাক্যের
বিভিন্ন পদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বা অন্বয় থাকা উচিত। এ ছাড়াও বাক্যের
অন্তর্গত বিভিন্ন পদ দ্বারা মিলিতভাবে একটি অখন্ড ভাব পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়া
প্রয়োজন, কেবলমাত্র তবেই তা বাক্য হবে।
একটি সার্থক বাক্যে কি কি গুণ থাকা উচিত?
ভাষার বিচারে বাক্যের নিম্নলিখিত তিনটি গুণ থাকা চাই। যেমন—
- (১) আকাঙ্ক্ষা
- (২) আসত্তি
- (৩) যোগ্যতা
বাক্যে আকাঙ্ক্ষা কাকে বলে?
(১) আকাঙ্ক্ষা – বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর আরেক পদ
শোনার যে ইচ্ছা তাকে আকাঙ্ক্ষা বলে। যেমন:
চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে
— এটুকু বললে বাক্যটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে না; আরো শোনার ইচ্ছা থাকে।
সুতরাং বাক্যটি এভাবে পূর্ণ করা যায়:
চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।
এভাবে বললে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট হয় এবং বোঝা যায় এবং এতে বাক্যেটি পূর্ণতা পায়।
বাক্যে আসত্তি কাকে বলে?
(২) আসত্তি — আসত্তি অর্থ - মিলন বা নৈকট্য বা
পারস্পরিক সংযোগ। মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে শব্দগুলো এমনভাবে পর পর সাজাতে হবে
যাতে মনোভাব প্রকাশে কোনো বাধা না থাকে। বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল
পদবিন্যাসই আসত্তি। যেমন:
করে ১৯৭১ বাংলাদেশ অর্জন স্বাধীনতা সালে।
এই বাক্যটি আসত্তিহীন। কারণ এতে শব্দগুলো পর পর না সাজিয়ে অগোছালো করে সাজানোর
ফলে বাক্যের আসল মনোভাব বোঝা অসম্ভব। সুতরাং বাক্যটি এমন হওয়া উচিত ছিলো —
১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।
যা আসত্তিপূর্ণ বাক্য।
বাক্যে যোগ্যতা কাকে বলে?
(৩) যোগ্যতা — বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের বিশ্বাসযোগ্য ভাবসম্মিলনের নাম
যোগ্যতা। সাধারণ গদ্যের ক্ষেত্রে যোগ্যতার বিচার হয়, কাব্যের ক্ষেত্রে নয়। যেমন:
চাঁদে বসে মা তার সন্তানকে ছাদ দেখাচ্ছেন।
এটি গদ্যে ব্যবহৃত হলে যোগ্যতার ভুল হবে কিন্তু কাব্যে ব্যবহৃত হলে এটি সঠিক।
আবার,
বর্ষার রৌদ্র প্লাবনের সৃষ্টি করে।
বাক্যটি যোগ্যতাহীন কারণ রৌদ্র প্লাবন সৃষ্টি করে না। সুতরাং এটি এমন হওয়া উচিত
ছিলো—
বর্ষার বৃষ্টিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়।
তবেই তা যোগ্যতাপূর্ণ বাক্য হবে।
একটি বাক্য যোগ্যতাহীন বিবেচিত হওয়ার কারণসমূহ —
- (ক) রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা
- (খ) দুর্বোধ্যতা
- (গ) উপমার ভুল প্রয়োগ
- (ঘ) বাহুল্য–দোষ
- (ঙ) বাগধারার রদবদল
- (চ) গুরুচণ্ডালী দোষ
দুর্বোধ্যতা — অপ্রচলিত, কঠিন এবং দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের
যোগ্যতা গুণ নষ্ট হয়। যেমন:
তুমি আমার সাথে প্রপঞ্চ করেছো।
চাতুরী বা মায়া অর্থে প্রপঞ্চ ব্যবহার হয়েছে, কিন্তু বাংলা
‘প্রপঞ্চ’ শব্দটা অপ্রচলিত।
উপমার ভুল প্রয়োগ — ঠিকভাবে উপমা অলংকার ব্যবহার না করলে বাক্য তার
যোগ্যতা গুণ হারাবে। যেমন:
আমার হৃদয় মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হলো।
বীজ ক্ষেতে বপন করা হয়, মন্দিরে নয়। কাজেই বাক্যটি এমন হওয়া উচিত ছিলো —
আমার হৃদয় ক্ষেতে আশার বীজ উপ্ত হলো।
বাগধারার রদবদল — বাক্যে বাগধারার রদবদল করলে বাক্য তার যোগ্যতার গুণ
হারিয়ে ফেলে। যেমন:
অরণ্যে রোদন = নিষ্ফল আবেদন
— এর পরিবর্তে যদি
বনে ক্রন্দন
ব্যবহার করি তবে বাক্যটি তার যোগ্যতা হারাবে।
গুরুচণ্ডালী দোষ — তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের ব্যবহারে কখনো কখনো
গুরুচণ্ডালী দেষের সৃষ্টি হয়। এর ফলে বাক্য তার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। যেমন:
গরুর গাড়ি, শবদাহ, মড়াপোড়া
ইত্যাদির পরিবর্তনে যদি যথাক্রমে —
গরুর শকট, শবপোড়া, মড়াদাহ
ব্যবহার করা হয় তবে বাক্যে গুরুচণ্ডালী দোষের সৃষ্টি হবে।
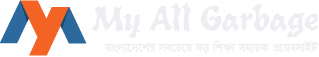
TNX ☺️
ReplyDelete